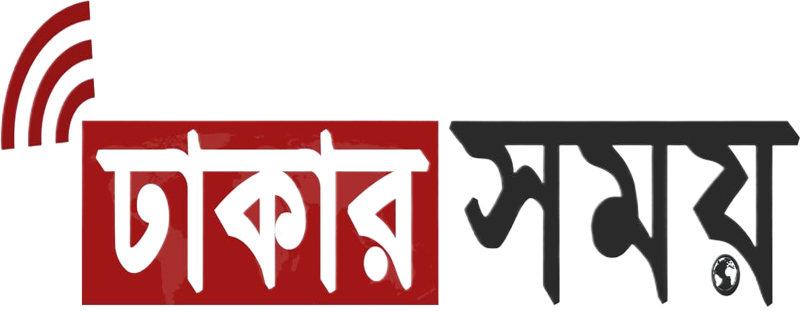
ড.রাধেশ্যাম সরকার
২৩ অক্টোবর, ২০২৫, 3:26 PM

মানবজীবনের অন্যতম মৌলিক চাহিদা হলো খাদ্য। কৃষিনির্ভর দেশ হিসেবে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনে গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। একসময় যেখানে খাদ্য ঘাটতি ছিল একটি বড় জাতীয় সংকট, আজ সেখানে উৎপাদনের দিক থেকে দেশ অনেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এই অগ্রগতি এক বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে, আর তা হলো খাদ্য অপচয়। দেশে প্রতি বছর ক্ষেত থেকে ভোক্তার প্লেটে যাওয়ার আগেই বিপুল পরিমাণ খাদ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ একই সময়ে লাখ লাখ মানুষ তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি এই অপচয় পরিবেশের ওপরও চাপ তৈরি করছে। খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত জমি, পানি, শ্রম ও অর্থ যখন অপচয়ের কারণে অকার্যকর হয়ে পড়ে, তখন তা টেকসই উন্নয়নকেও হুমকির মুখে ফেলে দেয়। এ বাস্তবতায় গবেষণাধর্মী আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা ও সমাধানের পথ খুঁজে বের করা জরুরি হয়ে পড়েছে।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, দেশে বছরে প্রায় ৪ কোটি ৭০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে ধানই প্রধান, যা তিন মৌসুম বোরো, আমন ও আউশে উৎপাদিত হয়ে থাকে। ধানের বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৪ কোটি টন। গম, ভুট্টা, ডাল ও তেলবীজও ক্রমশ বাড়ছে। আলুর উৎপাদন বছরে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টন ছাড়িয়েছে এবং ফল ও সবজির উৎপাদন দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ কোটি টনেরও বেশি। প্রাণিসম্পদ খাতে দেশ বড় ধরনের অগ্রগতি অর্জন করেছে। বর্তমানে বছরে প্রায় ২৩ বিলিয়ন ডিম, ১২ মিলিয়ন টন দুধ এবং ৪.৮ মিলিয়ন টন মাংস উৎপাদন হচ্ছে। মৎস্য খাতও সমৃদ্ধ হয়েছে, বছরে প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন টন মাছ আহরণ হচ্ছে, যা দেশের প্রাণিজ আমিষের বড় উৎস। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) জানিয়েছে, বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রধান খাদ্য উৎপাদনকারী দেশ। কিন্তু এই উৎপাদনের সাফল্য অনেকাংশেই ম্লান হয়ে যাচ্ছে অপচয়ের কারণে।
বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট হচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং উদ্বেগজনক। বিভিন্ন উৎসে অপচয়ের পরিমাণ ভিন্ন হলেও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এর তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৩৪% খাদ্য অপচয় হয়, যা অর্থনৈতিকভাবে প্রায় ২.৪ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের। অন্যদিকে, ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রামের (ইউএনইপি) ২০২৪ সালের ফুড ওয়েস্ট ইনডেক্স রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে বছরে প্রায় ২ কোটি ১১ লক্ষ টন খাদ্য অপচয় হয়। এই উচ্চ অপচয় শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবও ফেলে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) তথ্য অনুযায়ী, ধান কাটার পর ৮–১৫ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায়। ফল ও সবজির ক্ষেত্রে ক্ষতির হার আরও বেশি, প্রায় ২০–৪০ শতাংশ। এর আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বছরে প্রায় ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। শহরাঞ্চলে খাদ্য অপচয়ের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি। গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ ও গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রেস্তোরাঁ, সামাজিক অনুষ্ঠান ও পার্টিতে প্রতিদিন অনুমানিক কয়েকশ টন রান্না করা খাবার নষ্ট হয়। অন্যদিকে, গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের অপচয় অপেক্ষাকৃত কম হলেও ফসল কাটার পর সঠিক সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পরিবহনের অভাবে বিপুল পরিমাণ খাদ্য নষ্ট হয়ে যায়।
বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে অপচয়ের শতকরা হার বিভিন্ন উৎসে ৩৪৪৪% হিসেবে ধরা হয়; অর্থাৎ প্রতি ১০০ কেজি উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় ৩৪৪৪ কেজি অপচয় হচ্ছে। ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রামের (টঘঊচ) ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী দেশের খাদ্য অপচয়ের হার প্রায় ৪৪%, যা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।। প্রথমত, দেশে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষ তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অথচ তাদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য দেশে উৎপাদিত হয়। কিন্তু এই বিপুল খাদ্য অপচয়ের কারণে উৎপাদিত খাদ্য ভোক্তার কাছে পৌঁছাতে পারছে না, ফলে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা সমস্যার সমাধান অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে।
দ্বিতীয়ত, ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কাটার পর থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রায় ৮ থেকে ১৫ শতাংশ ধান নষ্ট হয়। এর পরিমাণ বছরে আনুমানিক ৩০ থেকে ৪৫ লাখ টন, যা জাতীয় খাদ্য মজুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নষ্ট হওয়ার সমান।
তৃতীয়ত, ফল ও সবজির ক্ষেত্রেও অপচয়ের মাত্রা অত্যন্ত বেশি। মোট উৎপাদনের প্রায় ২০ থেকে ৪০ শতাংশ ফল ও সবজি সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণের দুর্বলতার কারণে নষ্ট হয়ে যায়। এই অপচয়ের পরিমাণ বছরে প্রায় ৫০ থেকে ৮০ লাখ টন, যা দেশের কৃষকের শ্রম ও অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
চতুর্থত, ডিম, দুধ, মাছ ও মাংসের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যও অপচয়ের শিকার হয়। সংরক্ষণ ব্যবস্থার ঘাটতি, বিদ্যুৎ সংকট এবং অপর্যাপ্ত পরিবহন অবকাঠামোর কারণে এ খাতেও প্রায় ১৫ থেকে ২০ শতাংশ খাদ্যপণ্য নষ্ট হয়ে যায়। ফলে পুষ্টি ঘাটতি আরও প্রকট আকার ধারণ করে।
জাতিসংঘের তথ্যমতে, বিশ্বব্যাপী উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অপচয় হয়। বাংলাদেশেও এ হার প্রায় সমান। তবে বাংলাদেশের বাস্তবতা ভিন্ন, কারণ এখানে কৃষিজ সম্পদ সীমিত হলেও জনসংখ্যা ঘনবসতিপূর্ণ। ফলে খাদ্য অপচয়ের প্রভাব এ দেশে আরও ভয়াবহভাবে দেখা দেয় এবং খাদ্যনিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে।
খাদ্য অপচয় রোধে শুধু সরকারের পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়; কৃষক, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, সমাজ ও উন্নয়ন সহযোগীর সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। কৃষকদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি তারা আধুনিক প্রযুক্তি, ফসল কাটার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা (ঢ়ড়ংঃ-যধৎাবংঃ সধহধমবসবহঃ) এবং সঠিক সংরক্ষণ কৌশল ব্যবহার করেন, তাহলে উৎপাদিত খাদ্যের বড় অংশ নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে ফসল কাটার পর প্রায় ৩০৩৫ শতাংশ সবজি ও ফলমূল নষ্ট হয়, যা প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব। এছাড়া জিএপি (এড়ড়ফ অমৎরপঁষঃঁৎধষ চৎধপঃরপবং) অনুসরণ করলে কেবল উৎপাদনশীলতা নয়, সংরক্ষণযোগ্য খাদ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। কৃষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, কোল্ডস্টোরেজ সুবিধায় সহজ প্রবেশাধিকার এবং ন্যায্য দাম নিশ্চিত করা হলে তারা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে আরও উৎসাহিত হবেন, যা দীর্ঘমেয়াদে খাদ্য অপচয় হ্রাসে কার্যকর হবে।
ভোক্তাদের সচেতনতা খাদ্য অপচয় রোধে অপরিহার্য। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাদ্য ক্রয় বা রান্না না করা এবং অবশিষ্ট খাবার পুনর্ব্যবহার করার অভ্যাস গড়ে তোলা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারে সহায়ক। বিশেষ করে সচ্ছল শ্রেণিকে সতর্ক হতে হবে, কারণ তাদের মধ্যে অপচয়ের প্রবণতা বেশি। অতিরিক্ত রান্না বা অব্যবহৃত খাবার নিছক ফেলে না দিয়ে খাদ্যব্যাংক বা স্থানীয় দানমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে দরিদ্রদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। সমাজের সক্রিয় ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও সামাজিক সংগঠন মানুষকে সচেতন করতে পারে। “খাদ্য নষ্ট নয়, খাদ্য ভাগাভাগি” ধরনের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হলে খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হবে এবং অপচয় কমবে। নগর এলাকায় বিয়ে-অনুষ্ঠান, হোটেল ও রেস্তোরাঁয় সামাজিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে খাবার পরিকল্পিতভাবে পরিবেশন ও বিতরণ নিশ্চিত করা সম্ভব।
ব্যবসায়ীরাও খাদ্য অপচয় কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আধুনিক প্যাকেজিং, কোল্ড চেইন ও উন্নত লজিস্টিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করলে খাদ্যের স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধি পাবে। অতিরিক্ত খাদ্য ক্ষতিসাধক না করে খাদ্যব্যাংক, অনাথ আশ্রম বা আশ্রয়কেন্দ্রে দান করা যায়। সুপারশপ ও খুচরা বিক্রেতারা মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার আগে কম দামে বিক্রি করলে পণ্য নষ্ট হওয়ার আগে ব্যবহার হবে, যা ব্যবসায়িক আস্থা এবং টেকসই বাজার ব্যবস্থার জন্যও সহায়ক।
সরকারের পদক্ষেপ অপরিহার্য। খাদ্য সংরক্ষণ অবকাঠামো উন্নয়ন, পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ ও আধুনিক গুদাম নির্মাণ, কৃষি উৎপাদন ও বিপণনে উপগ্রহ চিত্র, এআই (অও) ও ডিজিটাল কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার প্রসার করা উচিত। হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাদ্য অপচয়ের সীমা নির্ধারণ এবং অবশিষ্ট খাদ্য দান বাধ্যতামূলক করার মতো আইন প্রণয়ন দরকার। কৃষকদের ন্যায্য বাজারমূল্য নিশ্চিত করা হলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে উৎসাহিত হবেন। জাতীয় কৌশল পরিকল্পনায় খাদ্য অপচয় রোধকে অগ্রাধিকার দিলে দেশের টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি সুফল বয়ে আনা সম্ভব হবে।
বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে খাদ্য অপচয়। প্রতি বছর উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট হওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষতি ছাড়াও এটি মানবিক সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ একই সময়ে প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষ খাদ্যের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে। খাদ্য অপচয় রোধে শুধুমাত্র সরকারের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়; কৃষক, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, নাগরিক সমাজ ও উন্নয়ন সহযোগীর সমন্বিত অংশগ্রহণ অপরিহার্য। কৃষককে আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সক্ষম করে তুলতে হবে, ভোক্তাদের সচেতন হতে হবে, ব্যবসায়ীদের দায়িত্বশীল ও উদ্ভাবনী হতে হবে এবং সরকারকে কার্যকর নীতিমালা ও পর্যাপ্ত অবকাঠামো দিয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে। নাগরিক সমাজকে সামাজিক আন্দোলন ও প্রচারণার মাধ্যমে খাদ্য অপচয় রোধে সক্রিয় করতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি অপচয় হওয়া খাদ্য মানে একটি মানুষের একবেলার আহার হারানো। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (ঝউএং) অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও দারিদ্র্য হ্রাসে খাদ্য অপচয় রোধ এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। খাদ্য উৎপাদনের সাফল্য তখনই অর্থবহ হবে, যখন প্রতিটি শস্য সঠিকভাবে মানুষের পাতে পৌঁছাবে।
লেখক: কৃষিবিদ, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও চেয়ারম্যান, ডিআরপি ফাউন্ডেশন।
ড.রাধেশ্যাম সরকার
২৩ অক্টোবর, ২০২৫, 3:26 PM

মানবজীবনের অন্যতম মৌলিক চাহিদা হলো খাদ্য। কৃষিনির্ভর দেশ হিসেবে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনে গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। একসময় যেখানে খাদ্য ঘাটতি ছিল একটি বড় জাতীয় সংকট, আজ সেখানে উৎপাদনের দিক থেকে দেশ অনেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এই অগ্রগতি এক বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে, আর তা হলো খাদ্য অপচয়। দেশে প্রতি বছর ক্ষেত থেকে ভোক্তার প্লেটে যাওয়ার আগেই বিপুল পরিমাণ খাদ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ একই সময়ে লাখ লাখ মানুষ তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি এই অপচয় পরিবেশের ওপরও চাপ তৈরি করছে। খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত জমি, পানি, শ্রম ও অর্থ যখন অপচয়ের কারণে অকার্যকর হয়ে পড়ে, তখন তা টেকসই উন্নয়নকেও হুমকির মুখে ফেলে দেয়। এ বাস্তবতায় গবেষণাধর্মী আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা ও সমাধানের পথ খুঁজে বের করা জরুরি হয়ে পড়েছে।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, দেশে বছরে প্রায় ৪ কোটি ৭০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে ধানই প্রধান, যা তিন মৌসুম বোরো, আমন ও আউশে উৎপাদিত হয়ে থাকে। ধানের বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৪ কোটি টন। গম, ভুট্টা, ডাল ও তেলবীজও ক্রমশ বাড়ছে। আলুর উৎপাদন বছরে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টন ছাড়িয়েছে এবং ফল ও সবজির উৎপাদন দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ কোটি টনেরও বেশি। প্রাণিসম্পদ খাতে দেশ বড় ধরনের অগ্রগতি অর্জন করেছে। বর্তমানে বছরে প্রায় ২৩ বিলিয়ন ডিম, ১২ মিলিয়ন টন দুধ এবং ৪.৮ মিলিয়ন টন মাংস উৎপাদন হচ্ছে। মৎস্য খাতও সমৃদ্ধ হয়েছে, বছরে প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন টন মাছ আহরণ হচ্ছে, যা দেশের প্রাণিজ আমিষের বড় উৎস। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) জানিয়েছে, বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রধান খাদ্য উৎপাদনকারী দেশ। কিন্তু এই উৎপাদনের সাফল্য অনেকাংশেই ম্লান হয়ে যাচ্ছে অপচয়ের কারণে।
বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট হচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং উদ্বেগজনক। বিভিন্ন উৎসে অপচয়ের পরিমাণ ভিন্ন হলেও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এর তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৩৪% খাদ্য অপচয় হয়, যা অর্থনৈতিকভাবে প্রায় ২.৪ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের। অন্যদিকে, ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রামের (ইউএনইপি) ২০২৪ সালের ফুড ওয়েস্ট ইনডেক্স রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে বছরে প্রায় ২ কোটি ১১ লক্ষ টন খাদ্য অপচয় হয়। এই উচ্চ অপচয় শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবও ফেলে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) তথ্য অনুযায়ী, ধান কাটার পর ৮–১৫ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায়। ফল ও সবজির ক্ষেত্রে ক্ষতির হার আরও বেশি, প্রায় ২০–৪০ শতাংশ। এর আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বছরে প্রায় ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। শহরাঞ্চলে খাদ্য অপচয়ের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি। গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ ও গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রেস্তোরাঁ, সামাজিক অনুষ্ঠান ও পার্টিতে প্রতিদিন অনুমানিক কয়েকশ টন রান্না করা খাবার নষ্ট হয়। অন্যদিকে, গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের অপচয় অপেক্ষাকৃত কম হলেও ফসল কাটার পর সঠিক সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পরিবহনের অভাবে বিপুল পরিমাণ খাদ্য নষ্ট হয়ে যায়।
বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে অপচয়ের শতকরা হার বিভিন্ন উৎসে ৩৪৪৪% হিসেবে ধরা হয়; অর্থাৎ প্রতি ১০০ কেজি উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় ৩৪৪৪ কেজি অপচয় হচ্ছে। ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রামের (টঘঊচ) ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী দেশের খাদ্য অপচয়ের হার প্রায় ৪৪%, যা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।। প্রথমত, দেশে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষ তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অথচ তাদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য দেশে উৎপাদিত হয়। কিন্তু এই বিপুল খাদ্য অপচয়ের কারণে উৎপাদিত খাদ্য ভোক্তার কাছে পৌঁছাতে পারছে না, ফলে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা সমস্যার সমাধান অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে।
দ্বিতীয়ত, ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কাটার পর থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রায় ৮ থেকে ১৫ শতাংশ ধান নষ্ট হয়। এর পরিমাণ বছরে আনুমানিক ৩০ থেকে ৪৫ লাখ টন, যা জাতীয় খাদ্য মজুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নষ্ট হওয়ার সমান।
তৃতীয়ত, ফল ও সবজির ক্ষেত্রেও অপচয়ের মাত্রা অত্যন্ত বেশি। মোট উৎপাদনের প্রায় ২০ থেকে ৪০ শতাংশ ফল ও সবজি সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণের দুর্বলতার কারণে নষ্ট হয়ে যায়। এই অপচয়ের পরিমাণ বছরে প্রায় ৫০ থেকে ৮০ লাখ টন, যা দেশের কৃষকের শ্রম ও অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
চতুর্থত, ডিম, দুধ, মাছ ও মাংসের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যও অপচয়ের শিকার হয়। সংরক্ষণ ব্যবস্থার ঘাটতি, বিদ্যুৎ সংকট এবং অপর্যাপ্ত পরিবহন অবকাঠামোর কারণে এ খাতেও প্রায় ১৫ থেকে ২০ শতাংশ খাদ্যপণ্য নষ্ট হয়ে যায়। ফলে পুষ্টি ঘাটতি আরও প্রকট আকার ধারণ করে।
জাতিসংঘের তথ্যমতে, বিশ্বব্যাপী উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অপচয় হয়। বাংলাদেশেও এ হার প্রায় সমান। তবে বাংলাদেশের বাস্তবতা ভিন্ন, কারণ এখানে কৃষিজ সম্পদ সীমিত হলেও জনসংখ্যা ঘনবসতিপূর্ণ। ফলে খাদ্য অপচয়ের প্রভাব এ দেশে আরও ভয়াবহভাবে দেখা দেয় এবং খাদ্যনিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে।
খাদ্য অপচয় রোধে শুধু সরকারের পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়; কৃষক, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, সমাজ ও উন্নয়ন সহযোগীর সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। কৃষকদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি তারা আধুনিক প্রযুক্তি, ফসল কাটার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা (ঢ়ড়ংঃ-যধৎাবংঃ সধহধমবসবহঃ) এবং সঠিক সংরক্ষণ কৌশল ব্যবহার করেন, তাহলে উৎপাদিত খাদ্যের বড় অংশ নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে ফসল কাটার পর প্রায় ৩০৩৫ শতাংশ সবজি ও ফলমূল নষ্ট হয়, যা প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব। এছাড়া জিএপি (এড়ড়ফ অমৎরপঁষঃঁৎধষ চৎধপঃরপবং) অনুসরণ করলে কেবল উৎপাদনশীলতা নয়, সংরক্ষণযোগ্য খাদ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। কৃষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, কোল্ডস্টোরেজ সুবিধায় সহজ প্রবেশাধিকার এবং ন্যায্য দাম নিশ্চিত করা হলে তারা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে আরও উৎসাহিত হবেন, যা দীর্ঘমেয়াদে খাদ্য অপচয় হ্রাসে কার্যকর হবে।
ভোক্তাদের সচেতনতা খাদ্য অপচয় রোধে অপরিহার্য। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাদ্য ক্রয় বা রান্না না করা এবং অবশিষ্ট খাবার পুনর্ব্যবহার করার অভ্যাস গড়ে তোলা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারে সহায়ক। বিশেষ করে সচ্ছল শ্রেণিকে সতর্ক হতে হবে, কারণ তাদের মধ্যে অপচয়ের প্রবণতা বেশি। অতিরিক্ত রান্না বা অব্যবহৃত খাবার নিছক ফেলে না দিয়ে খাদ্যব্যাংক বা স্থানীয় দানমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে দরিদ্রদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। সমাজের সক্রিয় ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও সামাজিক সংগঠন মানুষকে সচেতন করতে পারে। “খাদ্য নষ্ট নয়, খাদ্য ভাগাভাগি” ধরনের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হলে খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হবে এবং অপচয় কমবে। নগর এলাকায় বিয়ে-অনুষ্ঠান, হোটেল ও রেস্তোরাঁয় সামাজিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে খাবার পরিকল্পিতভাবে পরিবেশন ও বিতরণ নিশ্চিত করা সম্ভব।
ব্যবসায়ীরাও খাদ্য অপচয় কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আধুনিক প্যাকেজিং, কোল্ড চেইন ও উন্নত লজিস্টিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করলে খাদ্যের স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধি পাবে। অতিরিক্ত খাদ্য ক্ষতিসাধক না করে খাদ্যব্যাংক, অনাথ আশ্রম বা আশ্রয়কেন্দ্রে দান করা যায়। সুপারশপ ও খুচরা বিক্রেতারা মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার আগে কম দামে বিক্রি করলে পণ্য নষ্ট হওয়ার আগে ব্যবহার হবে, যা ব্যবসায়িক আস্থা এবং টেকসই বাজার ব্যবস্থার জন্যও সহায়ক।
সরকারের পদক্ষেপ অপরিহার্য। খাদ্য সংরক্ষণ অবকাঠামো উন্নয়ন, পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ ও আধুনিক গুদাম নির্মাণ, কৃষি উৎপাদন ও বিপণনে উপগ্রহ চিত্র, এআই (অও) ও ডিজিটাল কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার প্রসার করা উচিত। হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাদ্য অপচয়ের সীমা নির্ধারণ এবং অবশিষ্ট খাদ্য দান বাধ্যতামূলক করার মতো আইন প্রণয়ন দরকার। কৃষকদের ন্যায্য বাজারমূল্য নিশ্চিত করা হলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে উৎসাহিত হবেন। জাতীয় কৌশল পরিকল্পনায় খাদ্য অপচয় রোধকে অগ্রাধিকার দিলে দেশের টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি সুফল বয়ে আনা সম্ভব হবে।
বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে খাদ্য অপচয়। প্রতি বছর উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট হওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষতি ছাড়াও এটি মানবিক সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ একই সময়ে প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষ খাদ্যের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে। খাদ্য অপচয় রোধে শুধুমাত্র সরকারের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়; কৃষক, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, নাগরিক সমাজ ও উন্নয়ন সহযোগীর সমন্বিত অংশগ্রহণ অপরিহার্য। কৃষককে আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সক্ষম করে তুলতে হবে, ভোক্তাদের সচেতন হতে হবে, ব্যবসায়ীদের দায়িত্বশীল ও উদ্ভাবনী হতে হবে এবং সরকারকে কার্যকর নীতিমালা ও পর্যাপ্ত অবকাঠামো দিয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে। নাগরিক সমাজকে সামাজিক আন্দোলন ও প্রচারণার মাধ্যমে খাদ্য অপচয় রোধে সক্রিয় করতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি অপচয় হওয়া খাদ্য মানে একটি মানুষের একবেলার আহার হারানো। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (ঝউএং) অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও দারিদ্র্য হ্রাসে খাদ্য অপচয় রোধ এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। খাদ্য উৎপাদনের সাফল্য তখনই অর্থবহ হবে, যখন প্রতিটি শস্য সঠিকভাবে মানুষের পাতে পৌঁছাবে।
লেখক: কৃষিবিদ, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও চেয়ারম্যান, ডিআরপি ফাউন্ডেশন।